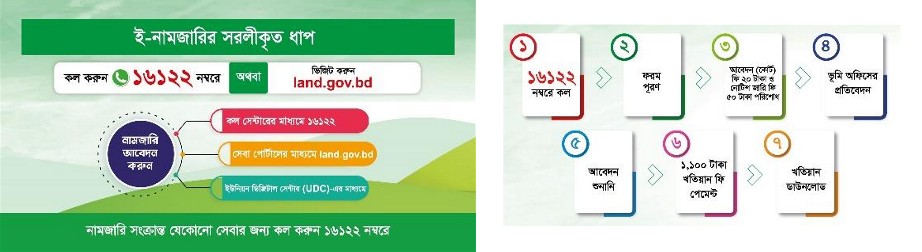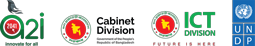-
-
-
-
জেলা সম্পর্কিত
জেলা পরিচিতি
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
অন্যান্য
-
জেলা প্রশাসন
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
শাখা সম্পর্কিত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ
স্থানীয় সরকার শাখা
কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
জেলা ই- সেবা কেন্দ্র
-
সরকারি অফিস সমূহ
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক
স্বাস্থ্য বিষয়ক
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
-
জেলা সমাজ সেবা অফিস
-
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র
-
জেলা যুব উন্নয়ন অফিস
-
জেলা সমবায় অফিস, মুন্সিগঞ্জ
-
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
-
জেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
-
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, মুন্সীগঞ্জ।
-
জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস, মুন্সিগঞ্জ
-
জেলা হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস
-
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ
-
জাতীয় মহিলা সংস্থা, জেলা অফিস, মুন্সিগঞ্জ
-
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ
-
জেলা রেজিস্ট্রার অফিস
আরও
অন্যান্য অফিসসমূহ
-
জেলা সমাজ সেবা অফিস
-
স্থানীয় সরকার
মুন্সীগঞ্জ জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি
-
সিরাজদিখান উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি ২০০৯-২০২৩ সাল
-
গজারিয়া উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি ২০০৯-২০২৩ সাল
-
মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
-
টঙ্গিবাড়ি উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
-
লৌহজং উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
-
শ্রীনগর উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
মিরকাদিম পৌরসভা
-
সিরাজদিখান উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি ২০০৯-২০২৩ সাল
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
লাইব্রেরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
-
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
-
কলেজসমূহ
-
ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজি, মুন্সিগঞ্জ
-
মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ
-
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ
-
মাদ্রাসাসমূহ
-
কারিগরি বিদ্যালয়
-
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
-
সরকারি হরগঙ্গা কলেজ
-
কে. কে. গভ: ইনস্টিটিউশন
-
মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়
-
প্রে.প্র.ড.ইয়াজউদ্দিন আ রে.ম.স্কুল এন্ড কলেজ
-
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডাটাবেস
সংস্থা/সংগঠন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
-
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
-
ই-সেবা কেন্দ্র
জেলা ই সেবা কেন্দ্র
জাতীয় ই সেবা
মোবাইল অ্যাপ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
- গ্যালারি
- জাতীয় সংগীত
- অনলাইন শুনানী
-
-
-
-
জেলা সম্পর্কিত
জেলা পরিচিতি
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
অন্যান্য
-
জেলা প্রশাসন
জেলা প্রশাসক
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
শাখা সম্পর্কিত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ
স্থানীয় সরকার শাখা
কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
জেলা ই- সেবা কেন্দ্র
-
সরকারি অফিস সমূহ
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক
স্বাস্থ্য বিষয়ক
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
- জেলা সমাজ সেবা অফিস
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র
- জেলা যুব উন্নয়ন অফিস
- জেলা সমবায় অফিস, মুন্সিগঞ্জ
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
- জেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, মুন্সীগঞ্জ।
- জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস, মুন্সিগঞ্জ
- জেলা হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস
- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ
- জাতীয় মহিলা সংস্থা, জেলা অফিস, মুন্সিগঞ্জ
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ
- জেলা রেজিস্ট্রার অফিস
আরও
অন্যান্য অফিসসমূহ
-
স্থানীয় সরকার
মুন্সীগঞ্জ জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি
- সিরাজদিখান উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি ২০০৯-২০২৩ সাল
- গজারিয়া উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি ২০০৯-২০২৩ সাল
- মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
- টঙ্গিবাড়ি উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
- লৌহজং উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
- শ্রীনগর উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি-২০০৯-২০২৩ সাল
মিরকাদিম পৌরসভা
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
লাইব্রেরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- কলেজসমূহ
- ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজি, মুন্সিগঞ্জ
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ
- মাদ্রাসাসমূহ
- কারিগরি বিদ্যালয়
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- সরকারি হরগঙ্গা কলেজ
- কে. কে. গভ: ইনস্টিটিউশন
- মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়
- প্রে.প্র.ড.ইয়াজউদ্দিন আ রে.ম.স্কুল এন্ড কলেজ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডাটাবেস
সংস্থা/সংগঠন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
-
ই-সেবা কেন্দ্র
জেলা ই সেবা কেন্দ্র
জাতীয় ই সেবা
মোবাইল অ্যাপ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
-
গ্যালারি
ফটোগ্যালারী
ভিডিও গ্যালারী
-
জাতীয় সংগীত
জাতীয় সংগীত (অডিও)
জাতীয় সংগীত (মিউজিক ট্র্যাক)
জাতীয় সংগীত (পাঠ)
THE NATIONAL ANTHEM RULES, 1978
-
অনলাইন শুনানী
মামলার তালিকা
এডমিন লগইন
অতীশ দীপঙ্করের পণ্ডিত ভিটা
অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত যিনি পাল সাম্রজ্যের আমলে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধধর্মপ্রচারক ছিলেন।

জন্ম
মহামহোপাধ্যায় সতীশ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতানুসারে পালযুগে মগধের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশ অঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তের সামন্তরাজ্য সহোর, যা অধুনা ভাগলপুর নামে পরিচিত, তার রাজধানী বিক্রমপুরীতে সামন্ত রাজা কল্যাণশ্রীর ঔরসে রাণী প্রভাবতী দেবীর গর্ভে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অতীশ দীপঙ্করের জন্ম হয়। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকের মতে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ।
শৈশব
ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। তিন ভাইয়ের মধ্যে অতীশ ছিলেন দ্বিতীয়। তার অপর দুই ভাইয়ের নাম ছিল পদ্মগর্ভ ও শ্রীগর্ভ। অতীশ খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেন। কথিত আছে তার পাঁচ স্ত্রীর গর্ভে মোট ৯টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।তবে পুন্যশ্রী নামে একটি পুত্রের নামই শুধু জানা যায়।
শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন মায়ের কাছে। তিন বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় পড়তে শেখা ও ১০ বছর নাগাদ বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ শাস্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারার বিরল প্রতিভা প্রদর্শন করেন তিনি। মহাবৈয়াকরণ বৌদ্ধ পণ্ডিত জেত্রির পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নালন্দায় শাস্ত্র শিক্ষা করতে যান।১২ বছর বয়সে নালন্দায় আচার্য বোধিভদ্র তাঁকে শ্রমণ রূপে দীক্ষা দেন এবং তখন থেকে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বোধিভদ্রের গুরুদেব অবধূতিপাদের নিকট সর্ব শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮ থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিক্রমশীলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপন্ডিত নাঙপাদের নিকট তন্ত্র শিক্ষা করেন। এরপর মগধের ওদন্তপুরী বিহারে মহা সাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণগিরি বিহারে গমন করেন এবং সেখানে প্রখ্যাত পন্ডিত রাহুল গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের আধ্যাত্নিক গুহ্যাবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করে ‘গুহ্যজ্ঞানবজ্র’ উপাধিতে ভূষিত হন।দীপঙ্কর ১০১১ খ্রিস্টাব্দে শতাধিক শিষ্যসহ মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ) গমন করেন এবং আচার্য ধর্মপালের কাছে দীর্ঘ ১২ বছর বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
তিব্বত যাত্রা
তিব্বতের সম্রাট ল্হ-লামা-য়েশো কয়েক জন দূতের হাতে প্রচুর স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বত ভ্রমনের আমন্ত্রন জানালে দীপঙ্কর সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে নিরাশ না হয়ে সম্রাট সীমান্ত অঞ্চলে সোনা সংগ্রহের জন্য গেলে গরলোগ অঞ্চলের অধিপতি তাঁকে বন্দী করেন ও প্রচুর সোনা মুক্তিপণ হিসেবে দাবী করেন। সম্রাট তাঁর পুত্র লহা-লামা-চং-ছুপ-ও কে মুক্তিপণ দিতে বারণ করেন এবং ঐ অর্থ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনানোর জন্য ব্যয় করতে বলেন। লহা-লামা-চং-ছুপ-ও সম্রাট হয়ে গুং-থং-পা নামে এক বৌদ্ধ উপাসককে ও আরো কয়েক জন অনুগামীকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনানোর দায়িত্ব দেন। এরা নেপালের পথে বিক্রমশীলা বিহারে উপস্থিত হন এবং দীপঙ্করের সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্ত সোনা নিবেদন করে ভূতপূর্ব সম্রাট ল্হ-লামা-য়েশোর বন্দী হওয়ার কাহিনী ও তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অভিভূত হন। আঠারো মাস পরে ১০৪০ খৃস্টাব্দে বিহারের সমস্ত দায়িত্বভার লাঘব করে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি দোভাষী সহ বারো জন সহযাত্রী নিয়ে প্রথমে বুদ্ধগয়া হয়ে নেপালের রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং নেপালরাজের আগ্রহে এক বছর সেখানে কাটান। এরপর নেপাল অতিক্রম করে থুঙ বিহারে এলে তাঁর দোভাষী ভিক্ষু গ্য-চোন-সেঙ অসুস্থ হয়ে মারা যান। ১০৪২ খৃস্টাব্দে তিব্বতে র পশ্চিম প্রান্তের ডংরী প্রদেশে পৌছন। সেখানে পৌছলে লহা-লামা-চং-ছুপ-ও এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করে তাঁকে থোলিং বিহারে নিয়ে যান। এখানে দীপঙ্কর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিপথপ্রদীপ রচনা করেন। ১০৪৪ খৃস্টাব্দে তিনি পুরঙে, ১০৪৭ খৃস্টাব্দে সম-য়ে বৌদ্ধ বিহার ও ১০৫০ খৃস্টাব্দে বে-এ-বাতে উপস্থিত হন।
তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার
দীপঙ্কর তিব্বতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট তান্ত্রিক পন্থার অপসারণের চেষ্টা করে বিশুদ্ধ মহাযান মতবাদের প্রচার করেন। তিনি তিব্বতে কদম-পা নামে এক লামা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।
রচনা
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তিব্বতের ধর্ম, রাজনীতি, জীবনী, স্তোত্রনামাসহ তাঞ্জুর নামে বিশাল এক শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা এবং কারিগরি বিদ্যা বিষয়ে তিব্বতী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন বলে তিব্বতীরা তাকে অতীশ উপাধীতে ভূষিত করে। অতীশ দীপঙ্কর অনেক সংস্কৃত এবং পালি বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। দীপঙ্করের রচিত গ্রন্থগলির মধ্যে বোধিপথপ্রদীপ, চর্যা-সংগ্রহপ্রদীপ, সত্যদ্বয়াবতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহগর্ভ, হৃদয়-নিশ্চিন্ত, বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলী, বোধিসত্ত্ব-কর্মাদিমার্গাবতার, শরণাগতাদেশ, মহযান-পথ-সাধন-বর্ণ-সংগ্রহ, শুভার্থ-সমুচ্চয়োপদেশ, দশ-কুশল-কর্মোপদেশ, কর্ম-বিভঙ্গ, সমাধি-সম্ভব-পরিবর্ত, লোকোত্তর-সপ্তকবিধি, গুহ্য-ক্রিয়া-কর্ম, চিত্তোৎপাদ-সম্বর-বিধি-কর্ম, শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময় ও বিমল-রত্ন-লেখনা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ইতালির বিখ্যাত গবেষক টাকি দীপঙ্করের অনেকগুলো বই আবিস্কার করেন।
মৃত্যু
তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মে সংস্কারের মতো শ্রমসাধ্য কাজ করতে করতে দীপঙ্করের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে ১০৫৪ খৃস্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতের লাসা নগরের কাছে চে-থঙের দ্রোলমা লাখাং তারা মন্দিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
তথ্যসূত্র
- ↑ "Portrait of Atisha [Tibet (a Kadampa monastery)] (1993.479)"। Timeline of Art History। New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–। October 2006। সংগৃহীত 2008-01-11।
- ↑ ২.০ ২.১ ২.২ ২.৩ তিব্বতে সওয়া বছর - রাহুল সাংকৃত্যায়ন, অনুবাদ - মলয় চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক - চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ISBN 81-85696-27-6
- ↑ ৩.০ ৩.১ "চন্দ্রগর্ভ থেকে শ্রীজ্ঞান" - ত্রৈমাসিক ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১২
- ↑ ৪.০ ৪.১ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের খোঁজে,অদিতি ফাল্গুনী, দৈনিক প্রথম আলো। ঢাকা থেকে প্রকাশের তারিখ: ২৬-০৯-২০১১ খ্রিস্টাব্দ।
- ↑ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, বাংলা বিশ্বকোষ। দ্বিতীয় খণ্ড। নওরোজ কিতাবিস্তান। ডিসেম্বর ১৯৭৫, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান। প্রথম খণ্ড। জানুয়ারি ২০০২।
- ↑ ৬.০ ৬.১ ৬.২ মুন্সিগঞ্জের বজ্রযোগিনী গ্রামে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের বাস্ত ভিটা,মো: রুবেল, বাংলাদেশ বার্তা ডট কম। ঢাকা থেকে প্রকাশের তারিখ: ৮ মার্চ,২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
- ↑ স্বামী অভেদানন্দের কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ - প্রকাশক- শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা ৭০০০০৬, ISBN 978-81-88446-83-4
ইদ্রাকপুর কেল্লা (Idrakpur Fort) মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত মোঘল স্থাপত্যের একটি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালিন বাংলার সুবাদার ও সেনাপতি মীর জুমলা ইছামতি নদীর তীরে ইদ্রাকপুর নামক স্থানে এই কেল্লাটি নির্মাণ করেন। ৮২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৭২ মিটার প্রস্থের ইটের তৈরি ইদ্রাকপুর কেল্লাটি মগ জলদস্যু এবং পর্তুগিজদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করা হয়।লোকমুখে প্রচলিত আছে ঢাকার লালবাগ কেল্লা থেকে ইদ্রাকপুর কেল্লা পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল। সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই কেল্লার প্রত্যেক কোণে বৃত্তাকার বেষ্টনী রয়েছে এবং দুর্গের একমাত্র খিলানাকার দরজা স্থাপন করা হয়েছে কেল্লার উত্তর দিকে। শত্রুর উদ্দেশ্যে গোলা নিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য ফোঁকর রয়েছে। পূর্ব দিকের মূল প্রাচীর দেয়ালের মাঝামাঝি একটি গোলাকার মঞ্চ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দুর্গেই দূর থেকে শত্রুর চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইদ্রাকপুর কেল্লার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে চারটি (ধলেশ্বরী, ইছামতী, মেঘনা এবং শীতলক্ষা) নদীর অবস্থান। ১৯০৯ সালে মোঘল স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন ইদ্রাকপুর কেল্লাকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তির মর্যাদা দেয়া হয়। প্রাচীর ঘেরা এই গোলাকার দূর্গটি এলাকায় এস.ডি.ও কুঠি হিসাবে পরিচিত।

শুলপুর গির্জা
মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের শুলপুর গ্রামে খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা একটি পবিত্র তীর্থস্থান। ১৭০০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের প্রথম দিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী কিছু গ্রাম থেকে কয়েকজন ক্যাথলিক খ্রিস্ট ভক্ত শুলপুরে এসে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীতে ১৮৬২ খ্রীঃ ইট সুরকির গাথনি দিয়ে ও ছনের চাল যুক্ত ১ম গীর্জাটি স্থাপন করা হয়। এরপর ১৯২২ খ্রীঃ টিনসেড গীর্জা নির্মান হয়। এরপর ১৯৬২ খ্রীঃ গীর্জাটির পুনঃ সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে ১১ই এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রীঃ আর্চবিশপ মাইকেল ডি রোজারিও বর্তমানের নব নির্মিত গীর্জাটি তৈরি করেন।

পোলঘাটা সেতু
প্রাচীন বাংলার গৌরবোজ্জ্বল স্থান শ্রীবিক্রমপুর মহানগরের একাংশ বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গৌরবময় উপাখ্যানের সাক্ষী অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন। এদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের পানাম পোলঘাটা গ্রামে অবস্থিত ইট ও সুরকি ব্যবহারে তৈরি মোগল আমলের পোলঘাটা সেতু এক অনন্য পুরার্কীতি। মুন্সীগঞ্জ জেলা শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে নির্মিত এই সেতু টঙ্গীবাড়ি উপজেলার সাথে জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বিক্রমপুর মহানগরের সীমানা পরিখা মির কাদিম খালের উপর তৈরি হওয়ার কারণে স্থানীয়দের নিকট এটি মীরকাদিম সেতু হিসাবেও পরিচিত। ৫২.৪২ মিটার দৈর্ঘ্যের ধনুকাকৃতি/অর্ধবৃত্ত গড়নের পোলঘাটা সেতুর নিচে খিলান দিয়ে নৌযান চলাচলের জন্য ৩টি স্থান রাখা হয়েছে। দুইপাশের নৌযান চলাচলের পথ মাঝখানের ফাঁকা স্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। পোলঘাটার ইটের পুলটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়ি
মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার শেখের নগর গ্রামে প্রায় দুইশত বছরের পুরনো রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়ি অবস্থিত। ইছামতি নদীর কোল ঘেঁষা শেখেরনগর রায় বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে কাছে ছায়া সুনিবির গ্রামে কালের সাক্ষী হয়ে রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়িটি যেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন অজানা কথা জানান দিয়ে যাচ্ছে। বর্গাকৃতির নকশার রায়ের বাড়ির দ্বিতল দালান ঘরের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট। দ্বিতল ভবনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে ২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থের একতলা বিশিষ্ট আরও ৩টি ভবন রয়েছে। রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আছে দুইটি শানবাধানো ঘাটের পুকুর।

পদ্মহেম ধাম
মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার দোসরপাড়া গ্রামে অবস্থিত পদ্মহেম ধাম ফকির লালন শাহের একটি আশ্রম। বাউল বাড়ি হিসেবে পরিচিত নৈসর্গিক এই স্থানে লালনের পদার্পণ না ঘটলেও প্রথম আলো পত্রিকার ফটো সাংবাদিক কবির হোসেন লালনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন। ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পাখ-পাখালির কলকাকলিতে পরিপূর্ণ পদ্মহেম ধামে প্রবেশ করতেই নজরে পড়বে লালনের অন্যতম নিদর্শন পাথরের তৈরি বিশাল একটি একতারা। মায়াময় প্রকৃতির মাঝে আরো নজরে পড়বে মুন্সীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কাঠের দোতলা ঘর, বৈঠকখানা ও লালনগীতি বিদ্যালয়। আশ্রমের পাশ দিয়ে তিনদিকে বাক নিয়ে চমৎকার মোহনার সৃষ্টি হওয়া ইছামতী নদী বহমান। আর তাই আশ্রম থেকে নদীর পাড়ে দাড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার দৃশ্য অনেক বেশী উপভোগ্য। ইছামতী নদী দিয়ে অধিকাংশ সময় নৌকায় সংসার গড়ে তোলা বেদেদের দল যেতে দেখা যায়। পদ্মহেম ধামে ক্যাম্পিং করে রাত্রিযাপন করা যায়।

শ্যামসিদ্ধির মঠ
শ্যামসিদ্ধির মঠ বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার শ্যামসিদ্ধি গ্রামে অবস্থিত একটি মঠ। আনুমানিক ২৪৭ বছরের পুরনো এই মঠটি ভারত উপমহাদেশের সর্বোচ্চ মঠ এবং সর্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ বলে বিবেচিত। ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত কুতুব মিনারের উচ্চতা ২৩৬ ফুট। আর শ্যামসিদ্ধির এই মঠটির উচ্চতা ২৪১ ফুট। অষ্টভুজ আকৃতির এই মঠের আয়তন দৈর্ঘ্যে ২১ ফুট ও প্রস্থে ২১ ফুট। তবে কুতুব মিনারের এর মত এটি সংরক্ষিত নয়, শ্যামসিদ্ধির মঠের এখন কেবল ধ্বংসাবশেষই অবশিষ্ট রয়েছে। মঠের গায়ের মূল্যবান পাথর এবং পিতলের কলসির এখন আর অস্তিত্ব নেই, এর মূল কাঠামো নকশা করা দরজা জানালা অনেক আগেই চুরি হয়ে গেছে। মঠের ভিতরে ৩ ফুট উচ্চতার কষ্টি পাথরের একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। বিক্রমপুরের ধর্নাঢ্য ব্যক্তি সম্ভুনাথ মজুমদার এই মঠটি নির্মাণ করেন। কথিত আছে সম্ভুনাথ স্বপ্নে তার পিতার চিতার উপরে মঠ নির্মাণের নির্দেশ পেলে তিনি এই মঠটি নির্মাণ করেন।

সোনারং জোড়া মঠ
মুন্সিগঞ্জ জেলা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে টঙ্গীবাড়ি উপজেলার সোনারং গ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সোনারং জোড়া মঠ। মঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও এটি মূলত একটি জোড়া মন্দির। মন্দিরের প্রস্থরলিপি অনুসারে, রুপচন্দ্র নামের এক হিন্দু বণিক ১৮৪৩ সালে বড় কালীমন্দির ও ১৮৮৬ সালে ছোট শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং ১৮৩৬ সালে শম্ভুনাথ নামের এক ব্যাক্তি এই মঠ স্থাপন করেন। কথিত আছে, এই মন্দিরেই শ্রী রুপচন্দ্রের শেষকৃত্য সম্পূন্ন হয়েছিল। প্রায় ২৪৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সোনারং জোড়া মঠভারত উপমহাদেশের সর্বোচ্চ মঠ হিসাবে খ্যাত। চুন সুরকি নির্মিত পুরো দেয়াল বিশিষ্ট এই মঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২১ ফুট এবং বড় মন্দিরের উচ্চতা ১৫ মিটার। মন্দিরের গোলাকার গম্বুজাকৃতি ছাদের শিখরে রয়েছে একটি ত্রিশূল। আর প্রত্যেক মূল উপাসনালয় ঘরের সাথে আছে একটি করে বারান্দা।

ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি
জমিদার যদুনাথ সাহা আনুমানিক ১৯০০ শতকে মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল গ্রামে ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি নির্মাণ করেন। যদুনাথ সাহা মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি বরিশাল থেকে লবণ, সুপারি, শাড়ি ইত্যাদি পণ্য আমদানি করে মুর্শিদাবাদে রপ্তানি করতেন। মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদার বাড়ির সাথে দুই তলা ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। ভবনের সামনে রয়েছে ৮ টি থাম, যা মূলত গ্রীক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট নির্দেশ করে। মূল ভবনের ভেতরের দেয়ালে ময়ূর, সাপ ও বিভিন্ন ফুল-পাখির নকশা অঙ্কিত রয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর
রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক বসতবাড়িকে ঘিরে জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর কমপ্লেক্সটিকে সাজানো হয়েছে। প্রায় ৩০ একর আয়তনের এই বাড়িতে অসংখ্য বৃক্ষরাজির ছায়াময় প্রকৃতির মাঝে বিভিন্ন পশুপাখির ম্যুরাল, কৃত্রিম পাহাড়-ঝরনা, শান বাঁধানো পুকুর ঘাট এবং দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য ত্রিকোণাকৃতির ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘরে জগদীশ চন্দ্র বসুর পোর্ট্রেট, বিভিন্ন গবেষণাপত্র, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তিতে লেখা চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠানো চিঠি এবং ১৭টি দুর্লভ ছবি প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে।
নাটেশ্বরের হারানো নগরী
মুন্সীগঞ্জের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে নাটেশ্বর প্রত্নতাত্তিক খননকৃত বৌদ্ধ মন্দির ও স্তুপ অন্যতম। টংগিবাড়ী উপজেলার সোনারং টংগিবাড়ী ইউনিয়নের নাটেশ্বর গ্রামে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের প্রত্নতাত্তিক খননে আবিস্কৃত হয় মন্দির এবং স্তুপ স্থাপত্যের অংশবিশেষ।সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে- অসাধারণ বৌদ্ধ মন্দির, তিনটি অষ্টোকোণাকৃতির স্তুপ, পিরামিড আকৃতির বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্তুপ, কেন্দ্রীয় মন্দির, হাজার বছর আগের রাস্তা, নালা প্রভৃতি।

রাজা বল্লাল সেনের দিঘী বা রামপালের দিঘী
বল্লাল সেন ধার্মিক (প্রচুর মন্দির গড়েন) এবং মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রজাদের পানীয় জলের কষ্ট দুর করতে চাইলেন। পরামর্শদাতার নাম রামপাল (রামপাল, পঞ্চবটি এই সব ঐতিহাসিক গ্রামগুলো এখনো টিকে আছে)। রাজা বল্লাল সেন ঘোষনা দিলেন একরাতের মাঝে তার মা যতোটা রাস্তা পায়ে হাটতে পারবেন উনি ততোবড় দীঘি খনন করবেন। রাজা ভেবেছেন বৃদ্ধা মা কতোটুকু আর হাটতে পারবে। রাতে রাজমাতার হাটা দেখে বল্লাল সেনের চক্ষু চরকগাছ। উনি হন হন করে হাটা শুরু করে বিশাল এলাকা ক্রস করে ফেললেন। ছলনার মাধ্যমে বল্লাল সেন মায়ের পথরোধ করলেন। পরে বিশাল এলাকা খনন করলেন। কিন্তু মায়ের সাথে ছলনার ফলে দিঘিতে পানি আসে না। বল্লাল সেনের সন্মনহানি হল প্রজাদের সামনে। মন্ত্রি রামপাল জানালেন দিঘিতে প্রান বিসর্জন দিলে পানি আসবে (দিনাজপুরের রাম সাগরের গল্পটাও অবিকল)। রাম সাগরের রাজা রাম নিজের প্রান বিসর্জন দিয়েছিলেন। বল্লাল সেনও তাই করতে গেলেন। কিন্তু রামপাল তার বন্ধুকে খুব ভালোবাসতেন। তাই বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে নিজের প্রান বিসর্জন দিলেন।

বাবা আদমের মসজিদ
মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালের অন্তর্গত রেকাবি বাজার ইউনিয়নের কাজী কসবা গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটি বহু গম্বুজবিশিষ্ট এবং ভূমি পরিকল্পনায় আয়তাকৃতির। এ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ১০.৩৫ মিটার × ৬.৭৫ মিটার এবং বহির্ভাগের পরিমাপ ১৪.৩০ মিটার × ১১.৪৫ মিটার। মসজিদটির দেয়াল ২ মিটার পুরু। মসজিদটিতে তিনটি ‘বে’ ও দুটি ‘আইল’ আছে। পশ্চিম দেয়ালের পশ্চাৎভাগ বাইরের দিকে তিন স্তরে বর্ধিত। পেছনের বর্ধিতাংশটি অতীব সুন্দর টেরাকোটা অলংকরণে নকশাকৃত। মিহরাবের মাঝখানে এবং পূর্ব ফাসাদে ঝুলন্ত শিকল ঘণ্টা ও ঝুলন্ত তক্তীর নকশা রয়েছে। তাছাড়া কুলুঙ্গির মাঝখানে বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান, জ্যামিতিক নকশা ও খিলান শীর্ষে ‘রোজেট’ নকশা লক্ষণীয়

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস